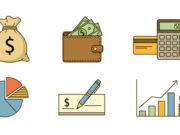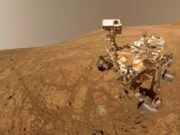আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে নানা ঘটনাপ্রবাহ ঘটছে। যদিও রাজনৈতিক মেরুকরণ এখনও চূড়ান্ত রূপ নেয়নি, তবুও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং জামায়াতে ইসলামীকে কেন্দ্র করে একটি নির্বাচনী জোট গঠনের প্রচেষ্টা চলছে।
এদিকে, কিছু দল সকল বিকল্প উন্মুক্ত রেখেছে, আদর্শিক স্পষ্টতার চেয়ে কৌশলগত নমনীয়তা বেছে নিচ্ছে, যা রাজনীতির বর্তমান প্রবণতার প্রতিফলন যেখানে কৌশল প্রায়শই নীতির চেয়ে বেশি। ১৯৪৭ সাল থেকে সমস্ত ঘটনার জন্য জামায়াত আমির শফিকুর রহমানের ক্ষমা চাওয়া এবং নির্বাচন-পরবর্তী জাতীয় সরকার গঠনের জন্য বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের অঙ্গীকার উভয়ই এই বৃহত্তর কৌশলগত খেলার অংশ।
জুলাই সনদের আইনি কাঠামো চূড়ান্ত হওয়ার আগে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) তে প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুমোদন করেছে। নীতিগতভাবে, এই সংশোধনীর অনেকগুলিই সমর্থনযোগ্য, যেমন প্রার্থীদের তাদের দেশীয় ও বিদেশী আয় ও সম্পদ প্রকাশের বাধ্যবাধকতা, গুরুতর অনিয়মযুক্ত নির্বাচনী এলাকায় ভোট বাতিল, পলাতকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত রাখা এবং ৫০,০০০ টাকার বেশি অনুদান ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রদানের বাধ্যবাধকতা।
এই বিধানগুলি নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে বলে মনে হচ্ছে।
তবে, কেবল অভিযোগপত্র দাখিল করলেই কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী না নির্দোষ তা আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার – নির্বাচন কমিশন বা সরকার নয়।
প্রার্থীদের জন্য জামানতের পরিমাণ ২০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০,০০০ টাকা করা অন্যায্য বলে মনে হচ্ছে। এতে সীমিত আর্থিক সামর্থ্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বাদ দেওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। নির্বাচন কমিশন কি ধরে নিয়েছে যে সমস্ত প্রার্থীকে ধনী হতে হবে?
সবচেয়ে বিতর্কিত এবং ব্যাপকভাবে সমালোচিত সংশোধনী হল এই বিধান যে, এমনকি যদি কোনও দল জোটের অংশ হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তবুও তার প্রার্থীদের দলের নিজস্ব নির্বাচনী প্রতীক ব্যবহার করতে হবে। এই ধরনের নিয়ম কার্যকর করে, কমিশন ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সামষ্টিক রাজনৈতিক কৌশল উভয়ের উপরই হস্তক্ষেপ করছে বলে মনে হচ্ছে। ইতিহাস থেকে কিছু উদাহরণ স্মরণ করা যাক: ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট জোট নৌকা প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল; ২০০১ সালে, বিএনপি-নেতৃত্বাধীন জোট – জাতীয় পার্টির একটি অংশ বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোট – বিভিন্ন দলের একাধিক প্রতীক ব্যবহার করেছিল। একইভাবে, ২০০৮ সালে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট নৌকা এবং লাঙ্গল উভয় প্রতীকেই প্রার্থী দিয়েছিল। এমনকি ২০১৮ সালেও, জামায়াত এবং বিএনপির বেশ কয়েকটি অনিবন্ধিত জোট কোনও সমস্যা ছাড়াই “ধানের শীষ” প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। তাহলে, হঠাৎ কেন এটি একটি সমস্যা হয়ে উঠবে?
জামায়াত “ধানের শীষ” প্রতীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল কারণ সেই সময়ে দলটির নিবন্ধন ছিল না। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত নয় এমন কোনও রাজনৈতিক দল কি আগামী নির্বাচনে কোনও নিবন্ধিত দলের সাথে জোট করলে নির্বাচনে কোনও নির্বাচনী প্রতীক পাবে না?
বিএনপির এই ধরনের নিয়ম অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি রয়েছে। দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ গতকাল প্রথম আলোকে বলেন যে তারা এই সংশোধনীর তীব্র বিরোধিতা করেন: “আরপিওর ২১ ধারা অনুযায়ী, জোটে নিবন্ধিত দলগুলি পূর্বে যেকোনো মিত্রের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত। আমরা এই ধারাটি বহাল রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। যদি এটি বাতিল করা হয়, তাহলে আমরা তা গ্রহণ করব না।”
তবে জামায়াত বিপরীত মত পোষণ করে। দলের নায়েবে-ই-আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের প্রথম আলোকে বলেন, “প্রত্যেক দলের নিজস্ব পরিচয় আছে এবং এর প্রতীক সেই পরিচয়কে প্রতিনিধিত্ব করে। তাই, নিবন্ধিত দলগুলির জন্য তাদের নিজস্ব প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই ভালো।”
অতীতের মতো জোটভুক্ত দলগুলিকে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে দিন যে তাদের জন্য কোনটি সবচেয়ে উপযুক্ত।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনের সাম্প্রতিক সংশোধনী জটিলতার আরও একটি স্তর যুক্ত করেছে। এতে বলা হয়েছে যে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত যে কেউ জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।
২০২৪ সালের জুলাইয়ের বিদ্রোহের সময় হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন নেতার (যাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে) বিরুদ্ধে এই আইনের অধীনে বিচার চলছে। প্রাক্তন মন্ত্রী ও এমপিসহ অনেক জ্যেষ্ঠ নেতা আত্মগোপনে রয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে খুন ও খুনের চেষ্টা থেকে শুরু করে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।
অনুমোদিত আরপিও খসড়ায় “আইন প্রয়োগকারী সংস্থা”-এর সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত করে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে – যার অর্থ সামরিক কর্মীদের এখন পুলিশের পাশাপাশি ভোটকেন্দ্রে মোতায়েন করা যেতে পারে, আলাদা আদেশের প্রয়োজন ছাড়াই।
এটি ব্যবহারিক এবং আইনি উভয় প্রশ্নই উত্থাপন করে। ১৫ জন কর্মরত সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক মামলাটি সেনাবাহিনীর মধ্যে কর্তব্যে অবহেলার কারণে নয় বরং বেসামরিক অভিযানে তাদের মোতায়েনের সময় মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। নির্বাচনও একটি বেসামরিক বিষয়। সশস্ত্র বাহিনীর কোনও সদস্য যদি নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের সময় অনিয়মের সাথে জড়িত হন, তাহলে কি তাদের বেসামরিক আইনের অধীনে বিচার করা হবে?
সেনাবাহিনীর সাংবিধানিক ভূমিকা হল জাতির সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং বহিরাগত হুমকি থেকে রক্ষা করা। অভ্যন্তরীণ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য তাদের মোতায়েন অনিবার্যবিতর্কের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।
তবুও বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য খুব কম বিকল্পই রয়েছে। তবুও, এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সশস্ত্র বাহিনীর নিরপেক্ষতা এবং পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শভাবে, আইন প্রয়োগের জন্য সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর না করেই বাংলাদেশের নির্বাচন পরিচালনা করতে সক্ষম হওয়া উচিত। যদিও এবার তা সম্ভব নাও হতে পারে, নীতিনির্ধারকদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে ভবিষ্যতের নির্বাচনগুলি এই ধরনের মোতায়েনের প্রয়োজন ছাড়াই অনুষ্ঠিত হতে পারে।
সোহরাব হাসান একজন সাংবাদিক এবং কবি। sohrabhassan55@gmail.com ঠিকানায় তার সাথে যোগাযোগ করা যাবে।