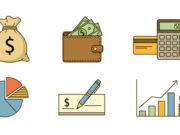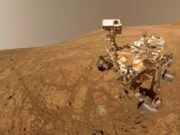জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর, বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক দৃশ্যপটের সামনে যে মূল প্রশ্নটি সামনে এসেছে তা হল কে ক্ষমতায় আসবে তা নয়, বরং দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো কেমন হবে তা হল। দীর্ঘদিন ধরে ঢাকার কেন্দ্রস্থলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা ক্ষমতার ভারসাম্য এখন পুনর্কল্পনা করা উচিত।
এই নতুন কাঠামোটি কেমন হবে? কেন্দ্র এবং প্রান্তিক অঞ্চলের মধ্যে সম্পর্ক কীভাবে পুনর্গঠিত হবে? এবং সাধারণ মানুষ – বিশেষ করে গ্রামীণ এবং প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষ – এর মধ্যে তাদের অভিজ্ঞতা, চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষার জন্য কীভাবে স্থান তৈরি করবে?
যদি গণতন্ত্রকে ভোটদানের বাইরে প্রসারিত করতে হয় এবং মানুষের দৈনন্দিন বাস্তবতাকে রূপ দিতে হয়, তাহলে এই প্রশ্নগুলির সমাধান করতে হবে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কারের মাধ্যমেই কেবল একটি অর্থপূর্ণ উত্তর পাওয়া যেতে পারে।
শুধুমাত্র নামে বিকেন্দ্রীকরণ
বাংলাদেশের উন্নয়নের আখ্যান প্রায়শই কেন্দ্রের সাফল্যের গল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ঢাকা-কেন্দ্রিক অর্থনীতি, নীতি নির্ধারণ, প্রশাসন এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় রাজনীতির স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। এই কাঠামোর মধ্যে, গ্রাম, উপজেলা (উপজেলা) এবং ইউনিয়নগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রের বাইরে থাকে।
প্রকৃতপক্ষে, কেন্দ্র এবং প্রান্তিকের মধ্যে তীব্র বৈষম্য একটি বৈষম্যমূলক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে টিকে আছে—যা এখনও ক্ষমতাহীন এবং কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল।
বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ঐতিহাসিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে বিকশিত হয়েছে। এটি কেবল নামে “বিকেন্দ্রীকরণ” করা হয়েছে কিন্তু কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ ছায়ায় গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে। গ্রামীণ ইউনিয়ন পরিষদ – প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে তৃণমূল প্রতিষ্ঠান – কার্যকরভাবে মন্ত্রণালয়ের একটি সম্প্রসারণ অফিসে পরিণত হয়েছে। এর বাজেট, প্রকল্প এবং এমনকি কর্মী নিয়োগ সবকিছুই ঢাকায় নির্ধারিত হয়।
সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার মতো নগর প্রতিষ্ঠানগুলি তুলনামূলকভাবে বেশি আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করে এবং তাদের সিদ্ধান্তগুলি আরও দ্রুত বাস্তবায়িত হয়—মূলত কারণ এগুলি কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকায় প্রতি নাগরিকের জন্য সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ গ্রামীণ ইউনিয়ন পরিষদের বাসিন্দার তুলনায় বহুগুণ বেশি।
তবুও জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ এখনও গ্রামে বাস করে, জন্ম নিবন্ধন থেকে শুরু করে বয়স্ক ভাতা এবং আবাসন প্রকল্প পর্যন্ত সবকিছুর জন্য ইউনিয়ন পরিষদের উপর নির্ভর করে। তবে, এই স্থানীয় সংস্থাগুলির বাজেট, কর্মী, প্রযুক্তি বা নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষের উপর কার্যত কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।
এই কাঠামো কেবল প্রশাসনিক নয় বরং রাজনৈতিক ক্ষমতাও প্রতিফলিত করে – যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কয়েকটি গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত, প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতা এবং চাহিদাকে প্রান্তিক স্তরে রেখে।
যদিও উপজেলা, ইউনিয়ন এবং জেলা পরিষদের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন, তাদের প্রকৃত কর্তৃত্ব অত্যন্ত সীমিত। বাজেট, উন্নয়ন প্রকল্প এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের চাবিকাঠি কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের হাতেই থাকে। ফলস্বরূপ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে জাতীয় নীতিতে তাদের চাহিদা এবং অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত করতে অক্ষম। এই কারণেই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রায়শই বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না – রাস্তাঘাট যেখানে ইতিমধ্যেই বিদ্যমান সেখানেই নির্মিত হয়, অন্যদিকে বন্যা সুরক্ষা বাঁধের তীব্র প্রয়োজন এমন এলাকাগুলি অবহেলিত থাকে।
রাজনৈতিক অর্থনীতির বাস্তবতা
এই অন্যায্য এবং অসম কাঠামো কেবল প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয় – এটি একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে ক্ষমতা, সম্পদ এবং প্রভাব কয়েকটি অভিজাত গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত। নব্য-মার্কসবাদী বিশ্লেষণে, রাষ্ট্রকে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষাকারী একটি হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয়। বাংলাদেশে, এই অভিজাত শ্রেণী কেবল অর্থনৈতিক নয়, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিকও। ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থান থেকে তারা রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টনের নিয়ম নির্ধারণ করে।
কেন্দ্রীভূত কাঠামোর অর্থ হলো ক্ষমতা কেবল কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সিদ্ধান্ত ঢাকায় নেওয়া হয়, কিন্তু এর প্রভাব প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে অনুভূত হয়। এই অভিজাতদের দখলের ফলে, স্থানীয় জনগণ – বিশেষ করে নারী, দরিদ্র এবং প্রান্তিক সম্প্রদায় – নীতি নির্ধারণ থেকে বাদ পড়ে। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং জেলা পরিষদের মতো প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলি সত্যিকার অর্থে অংশগ্রহণমূলক হতে পারে না, কারণ প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাদের হাতে থাকে না। গণতন্ত্র এভাবে ভোটদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণ কেবল প্রতীকী হয়ে ওঠে। স্থানীয় রাজনৈতিক জীবনে যে বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি এবং হীনমন্যতার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে তা এই কাঠামোগত অক্ষমতার প্রতিফলন।
তাহলে, কেন এই অসম কাঠামো এত দিন ধরে টিকে আছে? এর উত্তর রাজনৈতিক অর্থনীতির যুক্তিতে নিহিত। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পারস্পরিক নির্ভরতার একটি চক্র বিকশিত হয়েছে। রাজনীতিবিদরা প্রশাসন এবং সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চান, অন্যদিকে আমলারা নীতি ও প্রক্রিয়ার মালিকানা ধরে রাখতে চান। উভয় পক্ষই কেন্দ্রীকরণ থেকে উপকৃত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং আমলাতন্ত্রের জন্য, এই বৈষম্য একটি প্রণোদনা কাঠামো হিসেবে কাজ করে – এমন একটি ব্যবস্থা যা নিয়ন্ত্রণ, নিয়োগ, প্রকল্প,এবং সম্পদের বণ্টন।
অন্যদিকে, বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হবে সেই নিয়ন্ত্রণ হারানো। শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ এই কেন্দ্রীভূত শৃঙ্খলা বজায় রাখার সাথে গভীরভাবে জড়িত। অতএব, অসংখ্য সংস্কার প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও, সেগুলি খুব কমই বাস্তবায়িত হয়। বাস্তবে, বিকেন্দ্রীকরণের জন্য রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক অভিজাতদের একসাথে আবদ্ধ করে এমন ভাগ করা স্বার্থের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলা প্রয়োজন – এমন একটি রূপান্তর যা এখনও ঘটেনি। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংস্কারের ক্ষেত্রে এটিই মূল রাজনৈতিক বাধা।
সংস্কার কেন অপরিহার্য
এই বৈষম্যের পরিণতি প্রশাসনিক দুর্বলতার বাইরেও বিস্তৃত – এটি গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকেও দুর্বল করে। যখন মানুষ দেখে যে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই, তখন রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার জন্য তাদের প্রেরণা হ্রাস পায়। গণতন্ত্র তখন একটি উপর থেকে নীচের সম্পর্কে পরিণত হয়, যেখানে সাধারণ নাগরিকরা অংশগ্রহণকারীদের পরিবর্তে দর্শক হয়ে ওঠে।
অতএব, বাংলাদেশের জন্য যেকোনো নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্থানীয় সরকার সংস্কারকে কেন্দ্রে রাখতে হবে। সংস্কারকে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের বাইরে যেতে হবে – এতে ক্ষমতার পুনর্গঠন জড়িত থাকতে হবে যেখানে রাষ্ট্রীয় নীতি কেন্দ্র থেকে নয়, বরং প্রান্তিক মানুষের জীবিত অভিজ্ঞতা এবং চাহিদা থেকে শুরু হয়।
সংস্কারের অর্থ হলো, প্রথমত, আর্থিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা—স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলিকে তাদের নিজস্ব রাজস্ব তৈরি করার এবং উন্নয়ন বাজেটে সরাসরি প্রবেশাধিকার লাভের ক্ষমতা প্রদান করা।
দ্বিতীয়ত, এর জন্য প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন, যাতে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারা নির্বাচিত পরিষদের কাছে জবাবদিহি করতে পারেন, বিপরীতভাবে নয়।
তৃতীয়ত, সংস্কারকে বৃহত্তর রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে নাগরিকরা বাজেট প্রণয়ন, পরিকল্পনা এবং পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আন্তরিকতা
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কিছু সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত আবারও কেন্দ্র-সীমান্ত বৈষম্যের বিষয়টি সামনে এনেছে। উদাহরণস্বরূপ, চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবস্থাপনা একটি বিদেশী কোম্পানির কাছে হস্তান্তরের আকস্মিক সিদ্ধান্ত এমন এক সময়ে এসেছিল যখন বন্দরের কার্যক্রম সম্পর্কে কোনও বড় অভিযোগ ছিল না। এই ধরনের সিদ্ধান্ত স্থানীয় এবং জাতীয় উভয় পরামর্শ প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। একইভাবে, বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের শতাধিক কার্যকর সুপারিশ—যেমন পুলিশ সংস্কার এবং স্থানীয় সরকার সংস্কার—বাস্তবায়িত হয়নি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে: বিলম্ব কি কেবল প্রশাসনিক জটিলতার কারণে, নাকি এটি অদৃশ্য স্বার্থান্বেষীদের নীরব প্রতিরোধের ফলাফল?
একটি নতুন রাজনৈতিক কল্পনা: বিকেন্দ্রীকরণের পথ
গণঅভ্যুত্থানের পর আবির্ভূত “নতুন বাংলাদেশ”-এর জনপ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তব রূপ দিতে, বিকেন্দ্রীকরণের কোন বিকল্প নেই। ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভাগুলির আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা শক্তিশালী করতে হবে। স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রহ কর্তৃপক্ষ, প্রকল্প নির্বাচনে নাগরিকদের অংশগ্রহণ, বাজেট স্বচ্ছতা এবং নারী নেতৃত্বের সুযোগ – এই মূল নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে একটি নতুন সামাজিক চুক্তি তৈরি করতে হবে।
কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নীতি নির্ধারণ এবং সহায়তার হওয়া উচিত, নিয়ন্ত্রণ নয়। স্থানীয় প্রশাসন রাজনৈতিকভাবে জবাবদিহি এবং অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম না হলে, গণতন্ত্র রাজধানীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। গণঅভ্যুত্থান আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে গণতন্ত্রের প্রকৃত মাপকাঠি রাজধানীর রাজনীতিতে নয়, বরং প্রান্তিক মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার মধ্যে নিহিত।
সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সম্পদ বণ্টনে সমতা থাকলেই রাষ্ট্রের শক্তি টেকসই হয়। অতএব, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রার পরবর্তী পর্যায় হতে পারে একটি অংশগ্রহণমূলক বিকেন্দ্রীকরণ – যেখানে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সিটি কর্পোরেশন পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিক মনে করবে যে রাষ্ট্র সত্যিই তাদের।
কেন্দ্র এবং প্রান্তের মধ্যে ব্যবধান পূরণ করা কেবল স্থানীয় সরকার সংস্কারের একটি প্রশাসনিক কাজ নয় – এটি বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির নীলনকশা তৈরি করতে পারে, যেখানে উন্নয়ন এবং গণতন্ত্র উভয়ই নিচ থেকে উপরে পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।