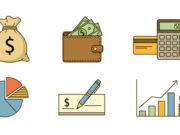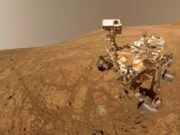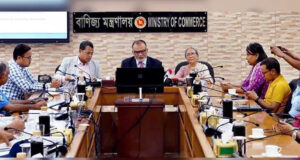জন্ম থেকেই আমরা একই প্রশ্ন শুনতে পাই: “কেমন আছো?” একই উত্তর আসে: “আমি ভালো আছি।” কিন্তু আমরা কি সত্যিই ভালো আছি? ভালো থাকার কি কোনও জায়গা আছে?
আমরা যেদিকেই তাকাই, সেখানেই অভাব। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। একবার বাড়লে, আর কখনও কমছে না। বেতন কমিশন, মহার্ঘ্য ভাতা—এই সুবিধাগুলি, কর্মক্ষম জনসংখ্যার সর্বোচ্চ ৫ শতাংশের জন্য প্রযোজ্য। আরও কমও হতে পারে। তাহলে, বাকিরা কীভাবে টিকে আছে? বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য, রাষ্ট্র অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে—কারণ প্রতিষ্ঠানটি তাদের চাহিদা পূরণ করে না।
যারা রাষ্ট্র থেকে উপকৃত হয়, তাদের জন্য নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু নির্বাচন আসলে কী? ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের মতে, এটি সমস্ত সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান। তারা বলে যে একটি নির্বাচিত সরকার থাকা সামাজিক স্থিতিশীলতা, আইন-শৃঙ্খলা এবং সুশাসন নিশ্চিত করে—সর্বত্র শান্তি ও শান্তি!
১৯৭৩ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত, আমরা ১২টি জাতীয় নির্বাচন প্রত্যক্ষ করেছি। যারা এই নির্বাচনের সুবিধা পেয়েছেন তারা সর্বদা তাদের প্রশংসা করেছেন। তারা দাবি করেছিল যে তারা জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েছে। এবং তাদের কাছে “ম্যান্ডেট” মানে যা খুশি করার স্বাধীনতা। এই প্রক্রিয়ায়, তারা সংবিধানকে পদদলিত করেছে, টুকরো টুকরো করেছে এবং ধ্বংসস্তূপে ফেলে দিয়েছে। প্রতিটি গোষ্ঠী তাদের শাসনের জন্য উপযুক্ত যেকোনো সংস্করণ পুনরুদ্ধার করতে চায়।
১৯৭৩ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আমরা ১২টি জাতীয় নির্বাচন প্রত্যক্ষ করেছি। যারা এই নির্বাচনের সুফল পেয়েছেন তারা সর্বদা তাদের প্রশংসা করেছেন। তারা দাবি করেছেন যে তারা জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েছেন। এবং তাদের কাছে “ম্যান্ডেট” মানে যা খুশি তাই করার স্বাধীনতা। এই প্রক্রিয়ায়, তারা সংবিধানকে পদদলিত করেছে, টুকরো টুকরো করেছে এবং ভেঙে ফেলেছে। প্রতিটি গোষ্ঠী তাদের শাসনের জন্য উপযুক্ত যেকোনো সংস্করণ পুনরুদ্ধার করতে চায়।
সংবিধান সম্পর্কে বলতে গেলে, একটা কথা অবশ্যই বলা উচিত—এটিকে প্রায়শই একটি পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই দেশে, “পবিত্র” বলে চিহ্নিত জিনিসের অভাব নেই। পবিত্র সংবিধান, সুপ্রিম কোর্টের পবিত্র হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র ভূমি, পবিত্র সংসদ। “পবিত্রতা”র আধিক্য রয়েছে। তবুও, একরকম, মনে হচ্ছে দেশটি একটি আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে—যার উপর বিভিন্ন গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই করছে।
আমরা যদি গত ১২টি নির্বাচনের একটি ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করি? মানুষ প্রায়শই সব ধরণের জিনিসের জন্য শ্বেতপত্র দাবি করে। নির্বাচনের জন্য কেন নয়? কিন্তু এমন কোনও প্রতিবেদন নেই। যারা নির্বাচনে “জয়ী” তারা বিশ্বাস করে যে তারা নির্দোষ ছিল—গণতন্ত্রের পাঠ্যপুস্তক উদাহরণ। তারা জোর দিয়ে বলে যে তাদের কাছে জনগণের ম্যান্ডেট আছে। কিন্তু তারা কি সত্যিই? আমরা যদি সংবাদপত্রগুলি স্ক্যান করি এবং জনগণের হৃদয়ের কণ্ঠস্বর শুনি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে এই নির্বাচনগুলি প্রতিনিধিত্বের চেয়ে আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ এবং লুণ্ঠনের অধিকার সম্পর্কে বেশি ছিল। যদি তা না হত, তাহলে আজ আমরা কেন একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছি?
এখন রাষ্ট্র, সংবিধান এবং নির্বাচন সবই এই প্রস্তাবিত “নতুন ব্যবস্থা”-এর মধ্যে আটকে আছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা কী? এটা এখনও স্পষ্ট নয়। শহুরে, বই পড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী এটিকে একভাবে ব্যাখ্যা করে; শহুরে দরিদ্র এবং গ্রামীণ কৃষকরা এটিকে ভিন্নভাবে বোঝে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উঠে আসা রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সুফি এবং চিন্তাবিদরা এটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন যে তারা কেবল সত্যের অধিকারী – মানব মুক্তির চূড়ান্ত প্রতিকার তাদের হাতে। যদি জাতি কেবল তাদের ধারণা অনুসরণ করে, তবে এটি একটি স্বর্গে পরিণত হত। তাদের ইশতেহার, বক্তৃতা এবং আদর্শিক কাঠামো রয়েছে। কিন্তু এখন, সেই ইশতেহার এবং বক্তৃতাগুলি নিজেই বিশৃঙ্খলার উৎস হয়ে উঠেছে। কেউ অন্যের সাথে একমত নয়। এটি সমাধানের জন্য, তারা বলে, নির্বাচন নাগরিকদের সিদ্ধান্ত নিতে দেবে যে তারা কোন পথ পছন্দ করে।
কিন্তু যারা নির্বাচন থেকে উপকৃত হবে না তাদের তূণেও তীর রয়েছে। তারা দাবি করে যে নির্বাচন মুক্তির পথ নয়। একটি নির্বাচন কেবল একটি দলকে অন্য দলে প্রতিস্থাপন করে – যেমন জ্বলন্ত চুলা থেকে ফুটন্ত পাত্রে ঝাঁপিয়ে পড়া। এই সবকিছুর অর্থ কী? তাদের যুক্তি, এখন আমাদের যা প্রয়োজন তা হল একটি বিপ্লবী সরকার।
কিন্তু যারা নির্বাচন থেকে উপকৃত হবে না তাদের তূণেও তীর আছে। তারা দাবি করে যে নির্বাচন মুক্তির পথ নয়। একটি নির্বাচন কেবল একটি দলকে অন্য দলে প্রতিস্থাপন করে – যেমন জ্বলন্ত চুলা থেকে ফুটন্ত পাত্রে ঝাঁপ দেওয়া। এই সবের অর্থ কী? এখন আমাদের যা প্রয়োজন, তারা যুক্তি দেয়, তা হল একটি বিপ্লবী সরকার।
১২টি নির্বাচনের পর, অবশেষে আমরা ২০২৪ সালের জুলাই মাসে একটি জনসাধারণের বিদ্রোহ দেখেছি।
কেউ কেউ এটিকে বিপ্লবও বলেছে। বলা হয় যে বর্তমানে ক্ষমতায় থাকা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সেই বিদ্রোহের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু এখন আমরা আসলে কী দেখতে পাচ্ছি?
যারা একসময় বিদ্রোহের সময় পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল তারা এখন বিভিন্ন উপদলের মধ্যে বিভক্ত। তারা কেবল একে অপরের সমালোচনা করছে না – তারা একে অপরকে সরাসরি ভেঙে ফেলছে। প্রাক্তন মিত্ররা তীব্র শত্রুতে পরিণত হয়েছে। মাত্র এক বছর কেটে গেছে, এবং এই বিভক্তি সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিরোধী-চূড়ায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু কেন এটি ঘটেছে?
পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ২০২৪ সালের বিদ্রোহের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হওয়া সেই গোষ্ঠীটিই। তারা ধীরে ধীরে পুনরুত্থিত হচ্ছে — যেমন একটি কচ্ছপ সাবধানে খোলস থেকে মাথা বের করে তার চারপাশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে। আর এখন তারা বলছে, “আমরা আগে ভালো ছিলাম।”
সম্প্রতি, দুটি ঘটনা ঘটেছে যা আলোচনার দাবি রাখে।
প্রথমত, জাতীয় পার্টির মধ্যে একটি ফাটল। আমরা জানি এই দলটি একজন ব্যক্তিকে ঘিরে আবর্তিত হয়। চেয়ারম্যান ইচ্ছামত দলীয় পদ হস্তান্তর বা ছিনিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু এত কিছুর পরে, কিছু নেতা অবশেষে পরিণত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। তারা চেয়ারম্যানের ক্ষমতা খর্ব করার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। প্রতিক্রিয়ায়, চেয়ারম্যান তাদের বহিষ্কার করেন এবং দলীয় কমিটিতে রদবদল করেন। “অসন্তুষ্ট” নেতারা তাদের নিজস্ব কমিটি গঠন করেন এবং চেয়ারম্যানকে বহিষ্কার করার মতো পদক্ষেপ নেন। তাদের সাথে যোগ দেন জাতীয় পার্টির প্রাক্তন নেতারা যারা দীর্ঘদিন ধরে দলের মূলধারা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।
এরপর জাতীয় পার্টির সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে, একটি দল জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে দলীয় কার্যালয়ের দিকে ছুটে যায়। অদ্ভুতভাবে, তারা যমুনা (একটি প্রতীকী স্থান বোঝায়) বা আদালতে যাননি – তারা সরাসরি দলীয় কার্যালয়ে যান। আমি এই পদক্ষেপের অর্থ ঠিক বুঝতে পারছি না। সেখানে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ এবং সেনাবাহিনী, যারা ইতিমধ্যেই হতাশ ছিল, তারা নির্বিচারে মানুষকে মারধর করে। তারপর জাতীয় পার্টির অফিসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।
দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে, একটি উপ-জেলা।
নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি সংসদীয় সীমানা পুনর্নির্ধারণ করেছে, ভাঙ্গা থেকে দুটি ইউনিয়নকে অন্য একটি নির্বাচনী এলাকায় একীভূত করেছে। এর ফলে তীব্র বিক্ষোভ শুরু হয়। এবং যথারীতি, প্রতিবাদের অর্থ ভাঙচুর এবং গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরোধ করা, যার ফলে হাজার হাজার মানুষ ব্যাপক দুর্ভোগের শিকার হয়। একটি বিষয় স্পষ্ট: স্থানীয় নেতারা তাদের নির্বাচনী এলাকাকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পারিবারিক সম্পত্তির মতো বিবেচনা করেন। “আমার এলাকা” ধারণাটি খুবই শক্তিশালী। তারা যা বিবেচনা করে তাতে হস্তক্ষেপ করতে চান না
উদাহরণস্বরূপ, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের কথাই ধরুন, যিনি ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন। এটি ছিল সামরিক শাসনামলের সময়। জামায়াতে ইসলামী ছাড়া সকল দল এটি মেনে নিয়েছিল। আইয়ুব খান এমনকি জামায়াত নেতাদের জেলও দিয়েছিলেন। আমার মতে, এটি ছিল উপমহাদেশে তার সময়ের সবচেয়ে প্রগতিশীল আইন। এটি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে রয়ে গেছে।
*মহিউদ্দিন আহমেদ একজন লেখক এবং গবেষক
*প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব।